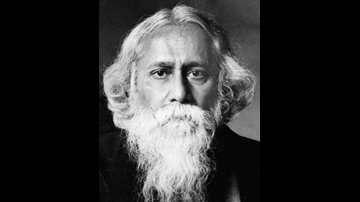রবীন্দ্রনাথের গানের শ্রোতাদের যেমন অনেক স্তর আছে তেমনি শিল্পীদের ক্ষেত্রেও তাই। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শিল্পীর নিজস্ব যোগ্যতা, অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা, সর্বোপরি তাঁর মেধা ও প্রতিভা অনুযায়ী অনুধাবনের উপরই তাঁর পরিবেশন করার সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয়। অনুধাবন করার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন স্তরের প্রশ্ন রয়েছে। প্রত্যেকটি মানুষ জন্মগতভাবে বিভিন্ন স্তরের মেধা ও প্রতিভা নিয়ে জন্মায়; পরবর্তীতে তাঁর পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়লব্ধ জ্ঞানে তিনি নিজের উৎকর্ষ সাধন করতে পারেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে সামগ্রিকভাবে তাঁর মেধার স্তর ও প্রতিভা অনুযায়ী সাধনালব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতাই তাঁকে যোগ্য করে তোলে এবং তাঁর অনুধাবন করার গভীরতাই তাঁর সঙ্গীতকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিতে পারে।
রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী অনুধাবন না করে সঙ্গীত পরিবেশন মূলতঃ একঘেয়েমী সৃষ্টি করে তা যতই সঙ্গীতের মৌলিক শর্ত পূরণ করুক না কেন। কারণ রবীন্দ্রনাথের গান সকল বাংলা গানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গভীর ভাবসম্পদ সমৃদ্ধ এবং তা এতটাই ঐশ্বর্যময় যে, প্রকৃত অনুধাবন ব্যতিরেকে সুনির্দিষ্ট একটি গানের সঙ্গতিপূর্ণ রস সৃষ্টি করা শিল্পীর পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।
মানুষের মধ্যে সহজাতভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তার মনে চলমান প্রতিক্রিয়া দৃশ্যমান হয় তার মুখাবয়বে। যেমন – দুঃখভারাক্রান্ত কিংবা বেদনাক্লিষ্ট মুখ, পক্ষান্তরে আনন্দিত মুখশ্রী, এভাবে রাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা, যন্ত্রণা ইত্যাদি; আবার গভীর সুখবোধ মানুষ সাধারণতঃ তার চেহারায় আড়াল করতে পারে না। ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথের গান যদি কোন শিল্পী সঠিকভাবে অনুধাবন করে পরিবেশন করতে সক্ষম হোন তাহলে শ্রোতার মানসপটে সুনির্দিষ্ট গানটির একটি বিমূর্ত চিত্র ফুটে ওঠে এবং শ্রোতা তখন সঙ্গীতের গভীর রসে নিমজ্জিত হয়ে অবগাহন করতে পারেন – যার ফলে শিল্পী ও শ্রোতা উভয়েই এক ধরনের ঐশ্বরিক অসীম আনন্দে হৃদয়ে পরম প্রশান্তি লাভে নিজেকে নতুন করে উজ্জীবিত করতে পারেন। এখানে উল্লেখ্য যে, দীর্ঘদিন ধরেই মানুষের দৈহিক ও মানসিক রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে ‘মিউজিক থেরাপী’ অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।
“আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে,/ সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।” রবীন্দ্রনাথের এই গানটি মোটামুটি ভাবে সকল রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীরাই জানেন এবং গেয়ে থাকেন বলে সাধারণভাবে ধারণা করা যায়। কিন্তু শতকরা কতজন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী নিজেকে সম্পূর্ণ অহংকারমুক্ত করতে পেরেছেন তা প্রশ্নাতীত নয়। তার মানে – বেশিরভাগ শিল্পীরাই গানটির মর্মার্থ যথাযথ অনুধাবন না করেই গাইছেন এবং হৃদয়ে আদৌ তা ধারণ করতেও ব্যর্থ হচ্ছেন।
সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সাফল্য কিংবা খ্যাতি সম্পূর্ণই কৌশলগত বিষয়। ‘সার্থক সঙ্গীত’ বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। সেটিই সার্থক সঙ্গীত যা মানুষকে অধিকতর মানুষ হতে সাহায্য করে, মানুষের অন্তর্গত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যকে অবদমিত রাখে, সৃষ্টির কল্যাণ ভাবনায় নিয়ত নিবেদিত রাখে। আর সেই সঙ্গীত সৃষ্টি তখনই সম্ভব হয় যখন একজন শিল্পী সঙ্গীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে গভীরভাবে অনুধাবন করে সঙ্গীতের মৌলিক শর্ত পূরণ সাপেক্ষে সঙ্গতিপূর্ণ রস সৃষ্টিতে পারঙ্গম হন।
রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা রক্ষা করা সহ কিছু জরুরী শর্ত পালনের বিকল্প নেই। অবশ্য এক্ষেত্রে শ্রোতা-দর্শকদের স্তর একটি বিবেচ্য বিষয়। সকল শ্রেণীর শ্রোতার জন্য পরিবেশন কৌশল ও অনুষঙ্গ এক হলে তা সর্বজনে সমাদৃত হবার সম্ভাবনা কম থাকে। তবুও একটি কথা অত্যন্ত আস্থার সাথে বলা যায় যে, যদি কোন শিল্পী সঙ্গীতের মৌলিক শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল রস সৃষ্টি করে বিমূর্ত শিল্প চিত্রায়িত করতে পারেন সেক্ষেত্রে অন্যান্য সকল শর্তই গৌণ হয়ে পড়ে।
রবীন্দ্রসঙ্গীতে যন্ত্রানুষঙ্গের বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। অপ্রাসঙ্গিক, অপরিপক্ক, সামঞ্জস্যহীন যন্ত্রানুষঙ্গ রবীন্দ্র সঙ্গীতকে এক ধরনের অনুধাবনহীন অন্তঃসারশূন্য স্থূল সঙ্গীতে রূপান্তরিত করে। যা প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি তথা রবীন্দ্রনাথকেই অসম্মান ও অশ্রদ্ধার নামান্তর মাত্র। আজকাল বেশিরভাগ রবীন্দ্রসঙ্গীতে তালবাদ্য সঙ্গতের পরিমিতিবোধের অভাব প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে – যা রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবকে নষ্ট করে।
আমরা মোটামুটিভাবে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে দেবতা তৈরী করে নিয়েছি। কিন্তু বাস্তব জীবনে পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মই যেমন মূল গ্রন্থ ও কল্যাণমুখী বাস্তবায়নের পরিপন্থী হয়ে অকল্যাণের পথে হাঁটছে ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথকে দেবতা বানিয়ে অন্তঃসারশূন্য পূজায় নিমগ্ন আছেন বেশিরভাগ রবীন্দ্র অনুরাগী ও শিল্পীরা। রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’ নাটক ও ‘চণ্ডালিকা’ গীতিনৃত্যনাট্যের মূল বক্তব্য অনুধাবন করার কোন ছাপ কি সমাজে বিদ্যমান? তাঁর চেতনা, দর্শন কিংবা মানব কল্যাণ ভাবনা ধারণ কিংবা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার কোন প্রয়োজনীয়তা কিংবা আগ্রহ কোনটিই আছে বলে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় না। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে এক ধরনের ‘ব্রাহ্মণ্যবাদ’ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নীরবে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত।
রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী একটি বিতর্কিত প্রসঙ্গ। কারো কারো মতে গুরু পরম্পরায় সুনির্দিষ্ট গায়কী গ্রহণ ও ধারণ করা আবশ্যকীয়। এখানে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক :
“যে মানুষ গান বাঁধিবে আর যে মানুষ গান গাহিবে – এ দু’জনই যদি সৃষ্টিকর্তা হয় তবে তো রসের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম।”
বিখ্যাত শিল্পী সাহানা দেবীর কণ্ঠে গান শুনে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন –
“সানু, তোমার গান যখন শুনি তখন মনে হয় আমার গান রচনা সার্থক হয়েছে; কেননা আমি দেখতে পাই ওখানে আমি যতখানি আছি তুমিও ততখানি আছো।”
এ দু’টো বক্তব্যে এটি অত্যন্ত পরিষ্কার যে, রবীন্দ্রনাথ শিল্পীকেও তাঁর গানের চূড়ান্ত রূপকল্প চিত্রায়নের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। সেক্ষেত্রে বাণী আর সুর সৃষ্টির পরে আর যেটি বাকী থাকে সেটি হচ্ছে গানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রস সৃষ্টি। আর সেই রস সৃষ্টি নির্ভর করে শিল্পী কতটা গভীরভাবে গানটির অন্তর্নিহিত ভাবকে অনুধাবন করতে পারলেন এবং গানটির বিমূর্ত চিত্রকল্প কতটা সফলভাবে চিত্রায়িত করতে পারলেন। সেই বিমূর্ত শিল্প সৃষ্টির একমাত্র শর্ত শিল্পীর নিজস্ব গায়কী – যা অন্যকে অনুকরণের মাধ্যমে সম্ভব নয় – ভাব কখনো আরোপিত হতে পারে না।
সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথকে অধ্যয়ন প্রকৃতই অসাধ্য না হলেও দুঃসাধ্য কিংবা কঠিন পরিশ্রমসাধ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে একটি ন্যূনতম পর্যায়ে না জেনে, না বুঝে রবীন্দ্রনাথের গান করা নিস্ফল প্রয়াস বৈ তো কিছুই নয়।
রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি অনুধাবনে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, তিনি আলোকিত মানুষ তৈরীর স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর গান সঠিকভাবে অনুধাবন করে অন্তরে গভীর উপলব্ধির মাধ্যমে মর্মার্থ ধারণ করতে পারলে যে কোন মানুষই অন্তর্গতভাবে নিজেকে আলোকিত করতে পারেন। একজন আলোকিত মানুষের অন্তঃকরণ পরিবারকে আলোকিত করতে পারে – ধারাবাহিকভাবে সমাজ আলোকিত হতে পারে।
পরিশেষে সকল রবীন্দ্র অনুরাগী ও শিল্পীদের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই – আমরা যেন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে প্রতিমা বানিয়ে পূজা না করে বরঞ্চ তাঁর সৃষ্টিকে গভীরভাবে অনুধাবন করে তার অন্তর্নিহিত আলোকিত সত্তার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই, স্রষ্টার পরম সঙ্গীতে উৎসর্গিত হই, নিবেদনে একনিষ্ঠ হই, মানব কল্যাণে ব্রতী হই।